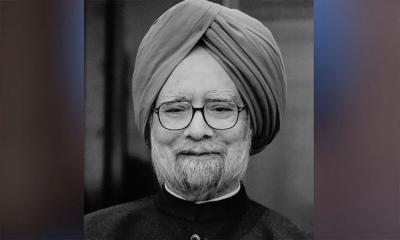- ঢাকা
- শুক্রবার, ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৪, ১২ পৌষ ১৪৩১

ঢাকা : শেখ মুজিবুর রহমান নামের মানুষটি আবাল্য রাষ্ট্র ও রাজনীতি নিয়েই ভাবনাচিন্তা করেছেন। শুধু অলস ভাবনাচিন্তা নয়, প্রচণ্ড সক্রিয়তা নিয়ে নিজের সমগ্র সত্তাকে দেশের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। সেই রাজনীতি তাকে নিয়ে গেছে ত্যাগের পথে, দুঃখ বরণের পথে। দুঃখ তাকে বিচলিত করতে পারেনি, দেশের দুঃখ বরণের ব্রত তার নিজের দুঃখকে তুচ্ছ করে দিয়েছে। রাজনৈতিক সংগ্রাম করে করেই তার দেশকে তিনি স্বাধীনতার উপল উপকূলে পৌঁছে দিয়েছেন, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্থপতি হয়েছেন এবং সেই স্বাধীন রাষ্ট্রটিকে আধুনিক ও প্রগতিশীল করে তোলার নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন, সে নীতিমালাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতেই আত্মবিসর্জন দিয়েছেন।
একটি নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাদান এবং রাষ্ট্রটির জন্য নীতিমালা ও তার প্রয়োগ-পদ্ধতি নির্ধারণ, এর পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল তার যে রাষ্ট্রচিন্তা, সেটির উৎস কী? এক কথায় এর দ্ব্যর্থহীন জবাব— ‘স্বদেশপ্রেম’। মুজিবের ছিল খাঁটি, নির্ভেজাল, নিরঙ্কুশ ও আপসহীন স্বদেশপ্রেম। সেই স্বদেশপ্রেম থেকেই তার রাষ্ট্রচিন্তার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছে। বইয়ের পাতা থেকে তিনি রাষ্ট্রচিন্তা আহরণ করতে যাননি কিংবা একান্ত মৌলিক বা অভিনব কোনো রাষ্ট্রচিন্তা দিয়ে পৃথিবীকে হকচকিয়ে দিতেও চাননি। ‘মুজিব মৌলিক চিন্তার অধিকারী বলে ভান করেন না। তিনি একজন রাজনীতির কবি, প্রকৌশলী নন। শিল্পকৌশলের প্রতি উৎসাহের পরিবর্তে শিল্পকলার প্রতি ঝোঁক বাঙালিদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। কাজেই সব শ্রেণি ও আদর্শের অনুসারীদের একতাবদ্ধ করার জন্য তার ‘স্টাইল’ (পদ্ধতি) সবচেয়ে বেশি উপযোগী ছিল।’
স্বদেশপ্রেমের আবেগেই তিনি প্রথম যৌবনে পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তার সবল কাণ্ডজ্ঞানের বলে পাকিস্তানের প্রতারণাটি তিনি ধরে ফেলতে পেরেছিলেন। স্বদেশপ্রেম মানে তো স্বদেশের মাটি, মানুষ, ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য— সবকিছুর প্রতিই প্রেম। সেসবের প্রতি সংগ্রাম ও তন্নিষ্ঠ দৃষ্টিপাতেই তিনি উপলব্ধি করে ফেললেন যে, পাকিস্তানের মতো একটি অদু্ভত ও কৃত্রিম রাষ্ট্রের থাবা থেকে মুক্ত করতে না পারলে তার স্বদেশের মুক্তিলাভ ঘটবে না। ’৪৮ সালে যখন বাঙালির ভাষার ওপর আঘাত এলো, তখন থেকেই বিষয়টি তার চেতনাকে আলোড়িত করতে শুরু করেছিল। হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত পাকিস্তান রাষ্ট্রটির পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে বৈষম্যের পাহাড় গড়ে বাংলাকে কার্যত উপনিবেশে পরিণত করে ফেলা, ’৫৪-এর বিপুল ভোটে নির্বাচিত যুক্তফ্রন্টের প্রতি পাকিস্তানি শাসকচক্রের অগণতান্ত্রিক আচরণ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার পাকিস্তানি অপপ্রয়াস, ’৫৮-এর সামরিক স্বৈরাচারের রাষ্ট্রীয় মঞ্চে অবতরণ— এসব কিছু দেখেশুনে শেখ মুজিব বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকেই তার রাজনৈতিক সংগ্রামের লক্ষ্যবিন্দুরূপে নির্ধারণ করে ফেলেছিলেন। তার সেই লক্ষ্যের কথাটি বোধহয় সর্বপ্রথম স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন ’৬১ সালের নভেম্বরে। অবশ্য একটি গোপন বৈঠকে। বৈঠকটি ছিল সে সময়কার গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে। আইয়ুবের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের নীতি ও কর্মপদ্ধতি স্থির করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সেই বৈঠকে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন মণি সিংহ ও খোকা রায় এবং আওয়ামী লীগের পক্ষে শেখ মুজিবুর রহমান ও তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। কমরেড খোকা রায় ‘সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও রাজবন্দিদের মুক্তিসহ মোট ৪টি জনপ্রিয় দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলা’র পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করলে শেখ মুজিব বলেন, ‘এসব দাবি-দাওয়া কর্মসূচিতে রাখুন, কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু দাদা, একটা কথা আমি খোলাখুলি বলতে চাই। আমার বিশ্বাস গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন— এসব কোনো দাবিই পাঞ্জাবিরা মানবে না। কাজেই স্বাধীনতা ছাড়া বাঙালির মুক্তি নেই। স্বাধীনতার দাবিটা আন্দোলনের কর্মসূচিতে রাখা দরকার।’ কমিউনিস্ট পার্টি নীতিগতভাবে স্বাধীনতার প্রস্তাব সমর্থন করলেও তাদের মতে তখনো সে রকম দাবি উত্থাপনের সময় হয়নি। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর শেখ মুজিব কমিউনিস্টদের বক্তব্যের সারবত্তা মেনে নেন, ভেতরে ভেতরে তিনি সেই চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ারই প্রস্তুতি নিতে থাকেন। তারই প্রমাণ পাই ছেষট্টির ছয়-দফা ঘোষণায়, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে ও একাত্তরের সেই দুনিয়া কাঁপানো দিন-মাসগুলোতে এবং ষোলো ডিসেম্বর যুদ্ধজয়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়। বাংলাদেশই হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ায় একমাত্র ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র। বাঙালির এই স্বাধীন রাষ্ট্রটিকে কেন্দ্র করেই এর স্থপতি বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রচিন্তার বহুমুখী উৎসারণ ঘটতে থাকে ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। যে জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা, সেই বাঙালির জাতিরাষ্ট্রটির প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাকে শুধু রাষ্ট্রভাষাই করা হলো না, বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘেও বাংলা ভাষাতেই ভাষণদান করলেন। এর ভেতর দিয়ে বলতে পারি, বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রচিন্তার একটি প্রতীকী প্রকাশ ঘটল। বাংলা ভাষাকে, বাংলা ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বাঙালি জাতিকে এবং বাংলার মানুষের আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠাদানই ছিল বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রচিন্তার মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যই তিনি তার নিজের মতো করে পথের সন্ধানে ব্রতী হন এবং এক্ষেত্রেও তার গভীর স্বদেশপ্রেম ও তীক্ষ কাণ্ডজ্ঞানই হয় সন্ধানী আলো।
বঙ্গবন্ধু একাত্তরের সাত মার্চের সেই অসাধারণ ও অবিস্মরণীয় ভাষণটি শেষ করেছিলেন যে বাক্যটি দিয়ে, সেটি ছিল— ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ নয় মাসে স্বাধীনতার সংগ্রাম শেষ হয়েছিল অবশ্যই। কিন্তু মুক্তির সংগ্রাম তো এত সহজে শেষ হওয়ার নয়। মুক্তির সংগ্রাম একটি স্থায়ী, দীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। সেই প্রক্রিয়ার অপরিহার্য অংশরূপেই বঙ্গবন্ধুর প্রবর্তনায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধানটি রচিত হয় এবং তাতে সংযোজিত হয় জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র— এই চারটি মৌলনীতি। এই নীতিগুলোর একটিও নিশ্চয়ই বঙ্গবন্ধুর মৌলিক উদ্ভাবন নয়, তবু এর প্রত্যেকটি সম্পর্কেই ছিল তার নিজস্ব অভিজ্ঞতাসঞ্জাত মৌলিক ভাবনা ও প্রয়োগ পদ্ধতি।
‘মুজিববাদ’-এর লেখক খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসের সাক্ষ্য থেকে আমরা বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে মোটা দাগের কিছু ধারণা পেয়ে যেতে পারি।
১৯৭২ সালেই খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসের ‘কতিপয় প্রশ্নের জবাবে’ নিজের চিন্তা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন— ‘ছাত্রজীবন থেকে আজ পর্যন্ত আমার এই সুদীর্ঘ কালের রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা ও সংগ্রাম কতিপয় চিন্তাধারার ওপর গড়ে উঠেছে। এদেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী তথা সব মেহনতি মানুষের জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি ও সাম্য প্রতিষ্ঠাই আমার চিন্তাধারার মূল বিষয়বস্তু। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে আমার জন্ম। কাজেই কৃষকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে আমি জানি শোষণ কাকে বলে। এদেশে যুগ যুগ ধরে শোষিত হয়েছে কৃষক, শোষিত হয়েছে শ্রমিক, শোষিত হয়েছে বুদ্ধিজীবীসহ সব মেহনতি মানুষ। এদেশে জমিদার, জোতদার, মহাজন ও তাদের আমলা-টাউটদের চলে শোষণ। শোষণ চলে ফড়িয়া ব্যবসায়ী ও পুঁজিবাদের। শোষণ চলে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের। এদেশের সোনার মানুষ, এদেশের মাটির মানুষ শোষণে শোষণে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের মুক্তির পথ কী? এই প্রশ্ন আমাকেও দিশেহারা করে ফেলে। পরে আমি পথের সন্ধান পাই। আমার কোনো কোনো সহযোগী রাজনৈতিক দল ও প্রগতিশীল বন্ধুবান্ধব বলেন শ্রেণিসংগ্রামের কথা। কিন্তু আমি বলি জাতীয়তাবাদের কথা। জিন্নাবাদ এদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিষবাষ্প। তার জবাবে আমি বলি, যার যার ধর্ম তার তার— এরই ভিত্তিতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কথা। শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সমাজতন্ত্র চাই। কিন্তু রক্তপাত ঘটিয়ে নয়— গণতান্ত্রিক পন্থায়, সংসদীয় বিধিবিধানের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করতে চাই সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। আমার এই মতবাদ বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থা ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করেই দাঁড় করিয়েছি। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, যুগোস্লাভিয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ পথে, নিজ নিজ অবস্থা মোতাবেক গড়ে তুলছে সমাজতন্ত্র। আমি মনে করি বাংলাদেশকেও অগ্রসর হতে হবে জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এই চারটি মূল সূত্র ধরে, বাংলাদেশের নিজস্ব পথ ধরে।’
স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে বেশ কিছুদিন বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রচিন্তা এরকমই ছিল। কিন্তু অচিরেই তিনি তার চিন্তায় মূলগত পরিবর্তন না ঘটিয়েই এর কিছুটা পুনর্বিন্যাস করতে বাধ্য হলেন। দেশের অভ্যন্তরের চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা ও সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রটির বিরুদ্ধে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রই বঙ্গবন্ধুকে অন্যভাবে ভাবতে বাধ্য করেছিল। সাম্রাজ্যবাদের অভিসন্ধি ও কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি এ সময়ে আরো গভীরভাবে সচেতন হয়ে ওঠেন। পৃথিবীটি যে শোষক ও শোষিত এই দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে— এ বিষয়টি তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করেন এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দেন— ‘আমি শোষিতের পক্ষে।’ এই উপলব্ধিজাত ঘোষণাকে নিজের দেশে বাস্তবে রূপায়িত করে তোলার জন্যই তিনি পূর্বঘোষিত ‘সংসদীয় বিধিবিধানের’ ‘গণতান্ত্রিক পন্থা’— অন্তত সাময়িকভাবে হলেও পরিহার করেন। অবশ্য ’৭২ সালে প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানটিতেও ব্রিটিশ ধাঁচের সংসদীয় বিধিবিধানের গোড়া অনুসৃত ছিল না। সেটিতেও গণতন্ত্রকে কণ্টকমুক্ত করা ও ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই ধর্মনিরপেক্ষতাবিরোধী রাজনৈতিক শক্তির অধিকার খর্ব করা হয়েছিল; পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক ভাবধারার পুনরুত্থানকে রোখার জন্যই ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু তাতেও খুব একটা কাজ হয়নি, বরং সাংবিধানিক নিষেধ বিধিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েই পাকিস্তানপন্থি সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার মর্মমূলে আঘাত হেনে যাচ্ছিল এবং এ কাজে বিভ্রান্ত বামদেরও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা পেয়ে গিয়েছিল। এরকম অবাঞ্ছিত বিব্রতকর পরিস্থিতিতেই বঙ্গবন্ধু গণতন্ত্রের প্রয়োগরীতিতে এক নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটালেন এবং তার নাম দিলেন ‘শোষিতের গণতন্ত্র’। এ ব্যবস্থায় সংসদীয় ও মন্ত্রিসভাশাসিত গণতান্ত্রিক কাঠামোর স্থলে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার এলো, বহুদলের বদলে একদলীয় পদ্ধতি প্রবর্তিত হলো এবং এরকম আরো বিধিবিধান জারি করা হলো, যেগুলোর সঙ্গে গণতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের এতদিনকার অভ্যস্ত ধারণা খাপ খায় না। তবে ষাটের দশক থেকে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাষ্ট্রনায়কদের নেতৃত্বে প্রায় অনুরূপ শাসন ও রাষ্ট্রনীতি চালু হয়ে গিয়েছিল। এর প্রতি দৃঢ় ও সক্রিয় সমর্থন ছিল সে সময়কার সোভিয়েত-নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের। এ ধরনের শাসনপ্রণালির নাম দেওয়া হয়েছিল ‘জাতীয় গণতন্ত্র’, অর্থনৈতিক বিচারে একে বলা হতো ‘অপুঁজিবাদী বিকাশের পথ’— অর্থাৎ ধনতন্ত্রকে এড়িয়ে সমাজতন্ত্র বিনির্মাণের পদ্ধতি।
জাতীয় গণতন্ত্র ও অপুঁজিবাদী বিকাশের তত্ত্ব-প্রচারকরূপে উলিয়ানভস্কি তখন বিশেষ খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিলেন। উলিয়ানভস্কি প্রচারিত তত্ত্বের কিংবা মিসর ও তানজানিয়াসহ তৃতীয় বিশ্বের কিছু কিছু দেশের শাসনপ্রণালির সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ‘শোষিতের গণতন্ত্র’ ও ‘দ্বিতীয় বিপ্লব’-এর কর্মসূচির কিছু কিছু সাযুজ্য থাকলেও মর্মবস্তু ও বহিরঙ্গ উভয় দিক থেকেই এর প্রকৃতি অনেক পরিমাণে স্পষ্ট স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত।
‘জাতীয় গণতন্ত্র’ নামে পরিচিত অনেকগুলো রাষ্ট্রের মতো বঙ্গবন্ধু ও সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীতে একদলীয় শাসনের বিধান সংযোজিত করেছিলেন বটে, কিন্তু তার নিজেরই এতে পুরোপুরি সায় ছিল বলে মনে হয় না। শামসুজ্জামান খান ১৯৭৫ সালের জুন মাসে ‘বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ’-এর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জানিয়েছেন যে, সে সময়ে তার ও প্রফেসর কবীর চৌধুরীর কাছে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন—
‘...ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাস, সারাজীবন গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করলাম, কত জেল খাটলাম আর এখন এক পার্টি করতে যাচ্ছি।... আমি এটা চাইনি। বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে।... অন্য কোনো পথ খোলা না দেখে আমি স্বাধীনতার পক্ষের লোকদের নিয়ে সমমনাদের একটি রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবে বাকশাল গঠন করছি। আমি সমাজতন্ত্রবিরোধী ধর্মনিরপেক্ষতাবিরোধী এবং সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধবিরোধী কোনো দল বা ব্যক্তিকে বাকশালে নেব না।... আমার ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য নয়, দেশকে বাঁচানোর জন্য এই পদক্ষেপ। আমি ক্ষমতা অনেক পেয়েছি, এমন আর কেউ পায়নি। সে ক্ষমতা হলো জনগণের ভালোবাসা ও নজিরবিহীন সমর্থন।... আমার এই একদলীয় ব্যবস্থা হবে সাময়িক। দেশটাকে প্রতিবিপ্লবের হাত থেকে রক্ষা করে আমি আবার গণতন্ত্রে ফিরে যাব। বহুদলীয় গণতন্ত্রে ফিরে যাব। তবে চেষ্টা করব আমার গণতন্ত্র যেন শোষকের গণতন্ত্র না হয়। আমার দুঃখী মানুষ যেন গণতন্ত্রের স্বাদ পায়।’
বঙ্গবন্ধু সত্যি সত্যিই আবার বহুদলীয় গণতন্ত্রে ফিরে যেতেন কি না, সে নিয়ে অলস জল্পনা-কল্পনা করা আজ একেবারেই অর্থহীন। তবে সন্দেহ নেই, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটিয়ে তিনি সমগ্র জনগণের জন্য গণতন্ত্রকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে চেয়েছিলেন। বিচারব্যবস্থার এমন সংস্কারের পরিকল্পনা করেছিলেন যাতে জনগণ অতি সহজে দ্রুত ন্যায়বিচার পেতে পারে। তার নিজের ভাষায়— ‘ইডেন বিল্ডিং বা গণভবনের মধ্যে আমি শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা ধরে রাখতে চাইনি। আমি আস্তে আস্তে গ্রামে, ইউনিয়নে, থানায়, জেলা পর্যায়ে এটা পৌঁছে দিতে চাই যাতে জনগণ তাদের সুবিধা পায়।’
‘শোষিতের গণতন্ত্র’ বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধুর চার দফা কর্মসূচির দিকে তাকালেই তার রাষ্ট্রচিন্তার মর্মকথাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেগুলো হচ্ছে— ১. বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম সমবায় গঠন; ২. মধ্যস্বত্বভোগী গ্রামীণ জোতদার, মহাজন, ধনিক বণিক শ্রেণির উচ্ছেদ; ৩. উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন শক্তির বিকাশ সাধন; ৪. আমলাতন্ত্রের বিলুপ্তি এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের ব্যাপক গণতন্ত্রায়ন। সমাজের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের জন্য বঙ্গবন্ধু সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছিলেন ‘বহুমুখী সমবায়’-এর ওপর। ’৭৫-এর ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে ওই সমবায় বা কো-অপারেটিভ সম্পর্কে অনেক কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, ‘পাঁচ বছরের প্ল্যানে বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রাম কো-অপারেটিভ হবে। প্রতিটি গ্রামে এই কো-অপারেটিভে জমির মালিকের জমি থাকবে। কিন্তু যে বেকার, প্রতিটি মানুষ, যে মানুষ কাজ করতে পারে তাকে কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। এগুলো বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে, টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিলের টাউটদের বিদায় দেওয়া হবে। তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এজন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে।’
বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও স্বাধীনতা একই সূত্রে গাঁথা তিনটি শব্দ। এই তিনটি শব্দ অবিচ্ছেদ্য এমন এক সত্তা, যা বাঙালি জাতির অস্তিত্ব। বঙ্গবন্ধু জন্ম না নিলে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি হতো কি না আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তার আজীবনের সংগ্রাম ছিল বাঙালির মুক্তি আর আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নই ছিল বাঙালিকে একটি স্বাধীন ভূখণ্ড দেওয়া। সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে তিনি বাঙালিকে ভালোবেসেছেন, কখনো বাঙালির অধিকার থেকে একবিন্দু পিছপা হননি। তিনি জাতির মহানায়ক। বাঙালির একমাত্র আশ্রয়স্থল হিসেবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।
লেখক : প্রগতিবাদী চিন্তাবিদ ও লেখক